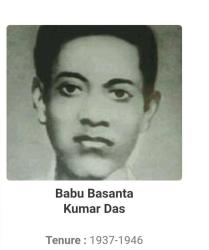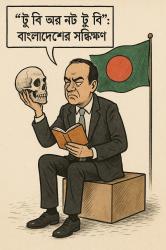রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধ কেন শেষ হচ্ছে না

সাইফুল খান
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আজ শুধু দুটি দেশের সংঘাত নয়। এটি হয়ে উঠেছে ২১ শতকের ভূরাজনীতির সবচেয়ে জটিল, বহুমাত্রিক ও কৌশলগত সংঘর্ষ। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে শুরু হওয়া রুশ আগ্রাসনের পর তিন বছর পার হয়ে গেলেও যুদ্ধের কোনো সুস্পষ্ট সমাপ্তির ইঙ্গিত নেই। মস্কো ও কিয়েভের যুদ্ধক্ষেত্র সীমিত ভূখণ্ডের হলেও, এর প্রতিধ্বনি এখন ইউরোপের নিরাপত্তা কাঠামো থেকে শুরু করে আমেরিকার বৈদেশিক নীতি, ন্যাটোর ঐক্য, চীনের ভূরাজনৈতিক কৌশল ও বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশ্ন উঠছে এই যুদ্ধ কেন শেষ হচ্ছে না? এর জবাব খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হয় রাশিয়া, ইউক্রেন, পশ্চিমা জোট ও আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার ভেতরে।
প্রথমত, রাশিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল ইউক্রেন দখল নয়, বরং একটি নতুন ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। মস্কোর কাছে এটি ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এক প্রতিরোধ যুদ্ধ। ভ্লাদিমির পুতিন বারবার বলেছেন, ইউক্রেনকে পশ্চিমা সামরিক ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত রাখা রাশিয়ার “অস্তিত্বগত নিরাপত্তা”র প্রশ্ন। আমেরিকার ‘Rand Corporation’-এর বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, পুতিন এমন এক যুদ্ধ চান যা দীর্ঘস্থায়ী হবে, যাতে ইউরোপ ক্লান্ত হয়, ন্যাটোর ঐক্য দুর্বল হয় এবং ইউক্রেন অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়ে। তাদের মতে, রাশিয়া জানে সরাসরি সামরিক জয়ে ইউক্রেন পুরোপুরি দখল সম্ভব নয়। কিন্তু যুদ্ধ দীর্ঘায়িত করে পশ্চিমা বিশ্বের আর্থিক ও রাজনৈতিক মনোযোগকে ক্লান্ত করে ফেলা ; এই কৌশলই এখন মস্কোর লক্ষ্য।
অন্যদিকে, ইউক্রেনের অবস্থান সম্পূর্ণ প্রতিরোধমূলক ও নৈতিক কাঠামোয় দাঁড়িয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি যুদ্ধকে ইউক্রেনের স্বাধীনতা ও পরিচয়ের লড়াই হিসেবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, যুদ্ধ থামলে ইউক্রেন তার সার্বভৌমত্ব হারাবে, তাই “যে কোনো মূল্যে প্রতিরোধ” এই মুহূর্তে দেশের একমাত্র পথ। ইউক্রেনের জন্য পশ্চিমা সহায়তা টিকে থাকা মানে অস্তিত্ব রক্ষা। কিন্তু যুদ্ধের দীর্ঘায়ন ইউক্রেনের অর্থনীতি ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ইউক্রেনের জিডিপি ৩০% এরও বেশি কমেছে এবং দেশটির জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বাস্তুচ্যুত। তবুও, কিয়েভ মনে করে যুদ্ধ থামালে মস্কোর কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে দেশটি। তাই তারা কূটনৈতিক সমঝোতার চেয়ে সামরিক প্রতিরোধকেই বেছে নিচ্ছে।
ইউরোপের অবস্থানও দ্বিধাগ্রস্ত। একদিকে তারা ইউক্রেনকে অর্থ, অস্ত্র ও রাজনৈতিক সহায়তা দিচ্ছে, অন্যদিকে জ্বালানি নির্ভরতা ও অর্থনৈতিক চাপ তাদের উদ্বিগ্ন করছে। জার্মানি, ফ্রান্সসহ অনেক ইউরোপীয় দেশ যুদ্ধের আর্থিক খরচে ক্লান্ত। ‘European Council on Foreign Relations (ECFR)’–এর এক জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ ইউরোপীয় নাগরিক এখন “শান্তির জন্য সমঝোতা”র পক্ষপাতী, “বিজয়ের জন্য যুদ্ধ” নয়। কিন্তু ইউরোপ জানে, যদি এখন ইউক্রেনকে ছাড় দেওয়া হয়, তবে এটি রাশিয়ার পরবর্তী আগ্রাসনের দরজা খুলে দেবে। তাই তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধের সহায়তায় যুক্ত রয়েছে।
আমেরিকার ভূমিকাই এই যুদ্ধের সবচেয়ে বিতর্কিত উপাদান। ওয়াশিংটন যুদ্ধকে “গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্রের সংঘাত” হিসেবে চিত্রিত করছে। তবে বাস্তবে এটি একটি প্রক্সি ওয়ার। যেখানে আমেরিকা রাশিয়াকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে চায়, সরাসরি যুদ্ধে না গিয়েই। আমেরিকান থিংকট্যাংক ‘Brookings Institution’ ও ‘Council on Foreign Relations (CFR)’ বিশ্লেষণ করেছে, যুক্তরাষ্ট্র ইউক্রেনকে দীর্ঘমেয়াদে “রাশিয়ার আফগানিস্তান” বানাতে চায়। অর্থাৎ এমন এক স্থায়ী সংঘাত, যা রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে রক্তক্ষরণ ঘটাবে। মার্কিন কংগ্রেসে সাহায্য প্যাকেজ নিয়ে বিতর্ক, বিশেষ করে রিপাবলিকানদের আপত্তি, দেখিয়ে দিয়েছে যে ওয়াশিংটনের মধ্যেও যুদ্ধ নিয়ে ঐক্য নেই। তবুও, রাশিয়াকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখতে আমেরিকা ইউক্রেনকে ছাড়ছে না।
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীন, ভারত, তুরস্ক ও আরব দেশগুলো এই সংঘাতে “কৌশলগত নিরপেক্ষতা” বজায় রেখেছে। চীন প্রকাশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে না গেলেও “শান্তি পরিকল্পনা”র নামে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দিচ্ছে, যা পশ্চিমা দেশগুলো অবিশ্বাসের চোখে দেখে। ভারতও রাশিয়ার জ্বালানি ও অস্ত্র আমদানি বজায় রেখে “স্ট্র্যাটেজিক অটোনমি” নীতি অনুসরণ করছে। এভাবে যুদ্ধটি এক ধরনের ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার খেলায় পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রত্যেকে নিজের কৌশলগত লাভের হিসাব করছে।
আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, যুদ্ধ এখন কৌশলগতভাবে অচলাবস্থায় (stalemate) পৌঁছেছে। সামরিক বিশ্লেষকরা বলছেন, ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণ (counteroffensive) ব্যর্থ হয়েছে, আর রাশিয়াও তার প্রাথমিক লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে ড্রোন, স্যাটেলাইট, আর্টিলারি এবং ট্রেঞ্চ যুদ্ধের এক মিশ্র রূপ তৈরি হয়েছে। যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে প্রযুক্তিনির্ভর কিন্তু স্থবির যুদ্ধ হিসেবে পরিচিত।
অর্থনৈতিকভাবে এই যুদ্ধের দীর্ঘায়ন বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানি সংকট ও খাদ্য নিরাপত্তার হুমকি তৈরি করেছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) বলছে, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে ২০২৩ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি কমেছে প্রায় ১%। কিন্তু মস্কো তার তেল রপ্তানির নতুন বাজার চীন, ভারত, তুরস্ক পেয়ে গেছে। ফলে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার প্রভাব সীমিত রাশিয়ার উপর ।
সবশেষে বলা যায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আসলে এক “কৌশলগত অচলাবস্থা”র দুনিয়া তৈরি করেছে। যেখানে কেউ পুরোপুরি জয়ী নয়, আবার পরাজয়ও স্বীকার করছে না। যুদ্ধ এখন হয়ে উঠেছে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক ক্লান্তির প্রতিযোগিতা। পশ্চিমা বিশ্ব চায় রাশিয়াকে দুর্বল করতে, রাশিয়া চায় নতুন বৈশ্বিক ভারসাম্য তৈরি করতে, আর ইউক্রেন লড়ছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য।
ফলে যুদ্ধের শেষ নেই, কারণ এটি আর কেবল ইউক্রেনের মাটিতে সীমাবদ্ধ নেই।এটি আজ বৈশ্বিক শক্তির পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্র এবং যতদিন এই ভারসাম্যের খেলা চলবে, ততদিন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধও চলবে। কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে, কখনো কূটনীতির টেবিলে আর কখনো বিশ্ব জনমতের প্রেক্ষাপটে।