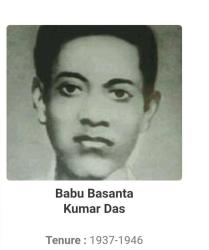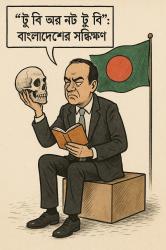বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা: নতুন প্রত্যাশা, পুরোনো চ্যালেঞ্জ ও আগামীর পথচলা!

নতুন প্রত্যাশা ও পুরোনো চ্যালেঞ্জের সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ
২০২৪ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর বাংলাদেশ এক নতুন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। একটি অভূতপূর্ব ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার এই পরিবর্তন কেবল একটি রাজনৈতিক ঘটনা নয়, বরং এটি দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত হতাশা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। এই পরিবর্তন দেশের প্রতিটি স্তরে এক নতুন প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছে: একটি দুর্নীতিমুক্ত, বৈষম্যহীন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে, যা আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও দেশীয় বিশ্লেষকদের কাছে একটি জটিল কিন্তু আশাব্যঞ্জক পরিস্থিতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
তবে, এই নতুন প্রত্যাশার পথ মোটেই মসৃণ নয়। অন্তর্বর্তী সরকার যে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, তা উচ্চ মূল্যস্ফীতি, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব, আর্থিক খাতের গভীর দুর্বলতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়ের মতো দীর্ঘস্থায়ী চ্যালেঞ্জে জর্জরিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, জ্বালানি সংকট ও ভূ-রাজনৈতিক চাপের মতো বাহ্যিক কারণসমূহ। তাই, নতুন সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো এই বহুবিধ সমস্যা মোকাবিলা করে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া। এটি কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার বিষয় নয়, বরং দেশের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করার একটি মৌলিক প্রক্রিয়া।
সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা: মূল্যস্ফীতির অদৃশ্য চাপ
রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সবচেয়ে বড় স্বস্তির প্রত্যাশা ছিল দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি থেকে মুক্তি। এটি কি পুরোপুরি পূরণ হয়েছে? কাগজে-কলমে হ্যাঁ, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালার কঠোর প্রয়োগের ফলে মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা কমেছে, যা সরকারিভাবে কিছুটা স্বস্তিদায়ক খবর। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, জুলাই ২০২৪-এ পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ১২ শতাংশে পৌঁছালেও, জুন ২০২৫ নাগাদ তা ৯ শতাংশের নিচে নেমে আসে এবং জুলাই ২০২৫-এ তা ৮.৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়।
কিন্তু এই পরিসংখ্যান সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতার সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কারণ মূল্যস্ফীতির হার কমার অর্থ এই নয় যে জিনিসপত্রের দাম কমে যাচ্ছে, বরং এর অর্থ হলো দাম বৃদ্ধির গতি ধীর হয়েছে। উচ্চ মূল্যের এই স্তর এখনো বিদ্যমান, যা নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম এখনো সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এটি জনগণের মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করছে। বাজার স্থিতিশীল হওয়ার সরকারি দাবি সত্ত্বেও, বাজারে গিয়ে মানুষ এখনো উচ্চ মূল্যের ধাক্কা অনুভব করছে। খাদ্য, জ্বালানি এবং বাসস্থানের মতো মৌলিক চাহিদাগুলোর খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় সীমিত আয়ের পরিবারগুলো সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে। এই পরিস্থিতি সমাজে হতাশা ও অসন্তোষের একটি বড় কারণ হিসেবে টিকে আছে।
অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতি: স্থিতিশীলতা ও শঙ্কার মিশ্র চিত্র
সামষ্টিক অর্থনীতির মূল সূচকসমূহ: জিডিপি, মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক খাত:
দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যে একটি মিশ্র চিত্র ফুটে ওঠে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) চূড়ান্ত হিসাবে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি ৪.২২ শতাংশ ছিল, যা গত চার বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এটি আগের সরকারের সাময়িক হিসাবে ধরা প্রবৃদ্ধির (৪.৫৯ বিলিয়ন ডলার) চেয়েও উল্লেখযোগ্যভাবে কম। অপরদিকে, বিবিএসের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়িয়েছে ৩.৯৭ শতাংশে। আন্তর্জাতিক মহলের পূর্বাভাসও প্রায় একই রকম। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) ২০২৫ সালের জন্য বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে ৩.৯ শতাংশ, যা ২০২৬ সালে ৫.১ শতাংশে উন্নীত হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছে।
মুদ্রাস্ফীতির উচ্চ হার দেশের অর্থনীতির জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ম্যাক্রো ট্রেন্ডস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশের বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ১০.৪৭ শতাংশ। তবে, অন্তর্বর্তী সরকারের কঠোর মুদ্রানীতির প্রয়োগের ফলে মুদ্রাস্ফীতির হারে কিছুটা নিম্নমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক আইএমএফ-এর নির্দেশনার অপেক্ষা না করেই একাধিকবার নীতি সুদহার বৃদ্ধি করেছে এবং বাজারে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ বন্ধ করে বিনিময় হারকে আরও নমনীয়ভাবে সমন্বয় করতে দিয়েছে। এর ফলে, জুলাই ২০২৫-এ মুদ্রাস্ফীতির হার ৮.৫৫ শতাংশে নেমে আসে, যা গত বছরের মে-জুনের ৯ শতাংশের বেশি হার থেকে নেমে এসেছে।
বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও রেমিট্যান্স প্রবাহ: আস্থার পুনরুদ্ধার
দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতিশীলতা একটি দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান সূচক। জুলাই ২০২৪-এ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ বিলিয়ন ডলারের নিচে নেমে গিয়েছিল, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ ছিল। তবে, এক বছরের ব্যবধানে, সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ এই রিজার্ভ বেড়ে ৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। এটি অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের একটি শক্তিশালী ইঙ্গিত। এই রিজার্ভ বৃদ্ধির পেছনে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর হুন্ডি, অর্থপাচার ও দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরায় রেমিট্যান্স প্রবাহে এক নতুন গতি এসেছে। একই সময়ে, আমদানি কমে যাওয়ায় ডলারের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে। এই দুইয়ের সম্মিলিত প্রভাবে বাজারে ডলারের সরবরাহ বেড়েছে, যা বাংলাদেশ ব্যাংককে ডলার বিক্রি না করে বরং বাজার থেকে কিনতে উৎসাহিত করেছে।
তবে, রিজার্ভের হিসাব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট (gross) রিজার্ভ যেখানে ৩১.৩৯ বিলিয়ন ডলার, সেখানে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) ব্যালেন্স অব পেমেন্টস অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পজিশন ম্যানুয়াল (বিপিএম৬) পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের প্রকৃত (net) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২৬.৪০ বিলিয়ন ডলার।
বিনিয়োগ পরিস্থিতি: সম্ভাবনা ও প্রতিবন্ধকতা
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পর বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই) প্রবাহে এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) নিট এফডিআই প্রবাহ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১৪.৩১ শতাংশ বেড়ে ৮৬৪.৬৩ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এটি বাংলাদেশের বিনিয়োগ সম্ভাবনার প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের ‘আস্থার প্রতীক’। সদ্য সমাপ্ত \'বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিট-২০২৫\'-এ প্রায় ৩ হাজার ১০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে, যা একটি অত্যন্ত ইতিবাচক দিক।
তবে, এই সম্ভাবনার পথকে পুরোপুরি মসৃণ বলা যায় না। ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত বিনিয়োগ পরিবেশ আরও অনুকূলে আনার আহ্বান জানিয়েছেন। এছাড়া, বাংলাদেশের সামনে সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক চ্যালেঞ্জটি হলো ২০২৬ সালে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণ। এর ফলে, শুল্কমুক্ত সুবিধা হারানোর কারণে রপ্তানি খাতে তীব্র প্রতিযোগিতা বাড়বে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রপ্তানি বহুমুখীকরণ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন বাজারে প্রবেশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেবে। এই প্রেক্ষাপটে, ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিংয়ের অব্যবস্থাপনা একটি বড় কৌশলগত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কার্গো গুদামের তীব্র সংকট, দক্ষ জনবলের অভাব এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা রপ্তানি প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। ব্যবসায়ীদের মতে, নির্দিষ্ট সময়ে পণ্য সরবরাহ করতে না পারলে ক্রেতারা পুরো চালান বাতিল করে দিতে পারেন, যা দেশের ভাবমূর্তি ও রপ্তানি আয় উভয়ের জন্যই হুমকি।
রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারের পথচলা: ম্যান্ডেট ও বাস্তবায়ন
অন্তর্বর্তী সরকারের ম্যান্ডেট: বিতর্ক ও বাস্তবতা:
অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা ও বৈধতা নিয়ে দেশে একটি চলমান বিতর্ক রয়েছে। যদিও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এই সরকারের আগমন ঘটেছে, তবে তাদের ক্ষমতা কি শুধুমাত্র নির্বাচন আয়োজন করা নাকি দেশের দীর্ঘমেয়াদি সমস্যাগুলো সমাধান করা—এ বিষয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। কিছু রাজনৈতিক দল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বিষয়ে (যেমন: চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশিদের হাতে দেওয়া, রাখাইনে মানবিক করিডোর, কাতারের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি) একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার অভিযোগ তুলেছে।
অধ্যাপক আইনুল ইসলাম অন্তর্বর্তী সরকারকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, তাদের প্রধান কাজ হলো নির্বাচন। তবে, সরকারের প্রেস সচিব এই ধারণার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে বলেছেন, এটি একটি ‘গণঅভ্যুত্থানের সরকার’ এবং এর ম্যান্ডেট ‘সবকিছু করার’। এই দ্বিমুখী অবস্থান প্রমাণ করে যে, সরকারের ভেতরে এবং বাইরে ম্যান্ডেট নিয়ে একটি দ্বিধাবিভক্ত অবস্থা রয়েছে, যা ভবিষ্যতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একটি সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে।
সুশাসন ও প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগ
অন্তর্বর্তী সরকার সুশাসন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। তারা সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করেছে এবং রাজস্ব বোর্ডের সংস্কারের জন্য একটি পরামর্শক কমিটি গঠন করেছে। দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন সহযোগীরা কর ও শুল্ক বিভাগকে আলাদা করার সুপারিশ করে আসছিল, যা বর্তমান সরকার কার্যকর করেছে। দুর্নীতি ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস করার বিষয়ে বিভিন্ন মহলের সুপারিশ রয়েছে, যা ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।
তবে, শুধুমাত্র নীতি প্রণয়ন যথেষ্ট নয়। সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৭২% ব্যবসায়ী কর কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং ৮২% বর্তমান কর ব্যবস্থাকে অন্যায্য মনে করে। এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে যে, প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি এবং জনসাধারণের আস্থার অভাব দূর করা আরও বড় চ্যালেঞ্জ।
আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি: উন্নতি নাকি অব্যাহত চ্যালেঞ্জ?
অন্তর্বর্তী সরকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিতে কঠোর অবস্থান নিয়েছে এবং এ লক্ষ্যে সেনাবাহিনী, পুলিশ ও বিজিবি সদস্যদের সমন্বয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে টার্গেট এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেছে। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা পরিস্থিতির উন্নতির দাবিও করেছেন।
তবে, সরকারি পদক্ষেপ সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি স্থিতিশীল হয়নি। বিগত এক বছরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাঁদাবাজি, গণপিটুনি (mob violence) ও কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাতসহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের প্রবণতা এখনো উচ্চ। এই বৈপরীত্যটি প্রমাণ করে যে, কঠোর নীতিগত সিদ্ধান্ত এবং মাঠ পর্যায়ে এর কার্যকর প্রয়োগের মধ্যে একটি ব্যবধান বিদ্যমান। যদিও পুলিশের কার্যক্রম এখন অনেক সক্রিয়, কিন্তু জনগণের মধ্যে অপরাধভীতি এখনো প্রবল। এটি অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।
ছাত্র ও যুব সমাজের ভবিষ্যৎ: সংকট ও সম্ভাবনা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন: একটি সফল আন্দোলন এবং তার পরবর্তী বাস্তবতা:
২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। এই আন্দোলনের মূল দাবিগুলো ছিল সুনির্দিষ্ট: নতুন কোটা আইন প্রণয়ন, আটক শিক্ষার্থীদের মুক্তি এবং হত্যাকারীদের বিচার নিশ্চিত করা। সরকার এই আন্দোলনের কিছু দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। শহীদদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং আহতদের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।
কিন্তু এই রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সত্ত্বেও, আন্দোলনের মূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক দাবিগুলো এখনো পুরোপুরি পূরণ হয়নি। যে তরুণ প্রজন্ম একটি সরকারের পতন ঘটিয়েছে, তারা এখন নতুন করে বৈষম্য ও হতাশার শিকার হচ্ছে। যে বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা এখনো অধরা। যে ছাত্রদের নামে মিথ্যা মামলা হয়েছিল, সেই মামলা এখনো পুরোপুরি প্রত্যাহার হয়নি। এই বেদনাদায়ক বাস্তবতা প্রমাণ করে যে রাজনৈতিক পরিবর্তন সহজ হলেও, গভীর-মূল সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার অনেক কঠিন।
বেকারত্বের হাহাকার: শিক্ষাব্যবস্থা ও চাকরির বাজারের ফারাক
বাংলাদেশের চাকরির বাজার বর্তমানে এক করুণ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে বেকারের সংখ্যা দেড় লাখ বেড়ে ২৭ লাখে দাঁড়িয়েছে। শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ক্রমাগত কমেছে এবং বিদেশে কর্মসংস্থানও ২২ শতাংশ কমে ১০ লাখে নেমে এসেছে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী তরুণ-তরুণীদের ২০ হাজার টাকার বেতনের চাকরি জোগাড় করতেও হিমশিম খেতে হচ্ছে।
এই বেকারত্বের মূল কারণ কেবল কর্মসংস্থানের অভাব নয়, বরং শিক্ষাব্যবস্থা ও শিল্প খাতের চাহিদার মধ্যে একটি মৌলিক অমিল। ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর মতে, শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে উঠছে না। উচ্চশিক্ষার মান বৈশ্বিকভাবে অনেক পিছিয়ে। গ্লোবাল নলেজ ইনডেক্সে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫৪টি দেশের মধ্যে ১২০তম এবং গ্লোবাল ট্যালেন্ট কম্পিটিটিভনেস ইনডেক্সে ১৩৪টি দেশের মধ্যে ১২৩তম। এই পিছিয়ে থাকা অবস্থা দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করছে। তরুণদের জন্য চাকরি তৈরি করার পাশাপাশি, শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে তারা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি ও প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মান: নতুন শিক্ষাক্রমের চ্যালেঞ্জ
নতুন শিক্ষাক্রম বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এতে পরীক্ষার চেয়ে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং নবম ও দশম শ্রেণিতে বিভাগ তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে, এর বিষয়বস্তু এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ও উদ্বেগ রয়েছে। শিক্ষাবিদরা মনে করেন, ভুল কন্টেন্ট ও চৌর্যবৃত্তির মতো বিষয়গুলো নতুন শিক্ষাক্রমকে অজনপ্রিয় করে তুলতে পারে।
এই শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা হলো শিক্ষা খাতে অপর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ। জিডিপির মাত্র ১.৫৩ শতাংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করা হয়, যা আন্তর্জাতিক মানের (৬ শতাংশ) অনেক নিচে। এই অপর্যাপ্ত বিনিয়োগের ফলে মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণার সুযোগ সীমিত হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে উচ্চশিক্ষার মানের ওপর। মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের বেতন কাঠামো দুর্বল হওয়ায় মেধাবী ব্যক্তিরা এই পেশায় আগ্রহী হচ্ছেন না।
সামাজিক সুরক্ষা ও জনস্বাস্থ্য: উন্নয়নের মানবিক দিক
স্বাস্থ্য খাতের দুর্বলতা: বাজেট, জনবল ও দুর্নীতি:
স্বাস্থ্য খাত বাংলাদেশের উন্নয়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু এটি দীর্ঘস্থায়ী দুর্বলতায় জর্জরিত। এই খাতে জিডিপির মাত্র ০.৭ শতাংশ ব্যয় হয়, যা বিশ্বমানের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। জনবল সংকট, দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা এই খাতের পুরোনো চ্যালেঞ্জ হিসেবে টিকে আছে। দেশের ১৭ কোটি জনসংখ্যার জন্য হাসপাতাল, ক্লিনিক ও প্রশিক্ষিত জনবল এখনো অপ্রতুল।
জাতিসংঘের একজন দারিদ্র্য বিশেষজ্ঞের মতে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা বা সামাজিক সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। এটি প্রমাণ করে যে, স্বাস্থ্যসেবা কেবল একটি খাত নয়, বরং এটি সুশাসনের একটি প্রতিফলন। অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং দুর্নীতির কারণে সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা অসম্ভব।
সামাজিক বৈষম্য ও অধিকারের প্রশ্ন
সামগ্রিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশে আয় বৈষম্য (বিশেষ করে শহরাঞ্চলে) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বহুবিধ দারিদ্র্য রয়ে গেছে। জাতিসংঘের একজন বিশেষজ্ঞের মতে, আদিবাসী, দলিত, বেদে, হিজড়া এবং ধর্মীয় ও ভাষাগত সংখ্যালঘুরা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক নয়, এটি সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি।
পাশাপাশি, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মতো দমনমূলক আইনের অধীনে সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, বিরোধী রাজনীতিবিদ এবং শিক্ষাবিদদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রয়োগের কারণে আটক করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিক মহলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যেও উদ্বেগ তৈরি করে। এই ধরনের দমনমূলক ব্যবস্থা দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।
সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগামীর পথচলা
একটি ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ বর্তমানে এক সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। অর্থনৈতিক সূচকগুলোতে স্থিতিশীলতা ফিরে আসা, বিশেষ করে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের শক্তিশালী হওয়া এবং এফডিআই প্রবাহে বৃদ্ধি—নতুন সরকারের জন্য এক বড় অর্জন। এই সাফল্য মূলত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে নেওয়া প্রাথমিক পদক্ষেপের ফল। তবে, এটি কেবল একটি প্রাথমিক ধাপ। সামনে দীর্ঘ পথ রয়েছে এবং এই পথচলায় গভীর কাঠামোগত সংস্কার প্রয়োজন।
বর্তমানে, উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বেকারত্ব, শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা, স্বাস্থ্য খাতের অব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির মতো চ্যালেঞ্জগুলো এখনো জনগণের জীবনকে প্রভাবিত করছে। এগুলো কেবল সরকারের একার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় একটি সম্মিলিত ও সুদূরপ্রসারী কৌশল গ্রহণ করা জরুরি, যেখানে সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ, ব্যবসায়ী সমাজ এবং ছাত্র সমাজেরও ভূমিকা থাকবে।
◑ সাধারণ জনগণের জন্য: সচেতনতা বৃদ্ধি, সরকারি নীতির সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা, এবং মিথ্যা তথ্য ও প্রপাগান্ডা থেকে নিজেদের রক্ষা করা।
◑ ব্যবসায়ী সমাজের জন্য: এলডিসি উত্তরণের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দক্ষতা উন্নয়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দুর্নীতি রোধে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করা।
◑ ছাত্র সমাজের জন্য: শুধুমাত্র প্রচলিত শিক্ষার ওপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রায়োগিক ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বারোপ করা। নিজেদের অধিকার ও সুশাসনের জন্য আন্দোলনকে একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় রূপ দেওয়া এবং দেশের নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা।
◑ সরকারের জন্য: সুশাসন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গবেষণায় জিডিপির অন্তত ৩-৪ শতাংশ ব্যয় করা এবং দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত সংস্কারের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা। শুধুমাত্র রুটিন কাজ নয়, বরং জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী একটি সত্যিকার অর্থে পরিবর্তনমুখী এবং জনবান্ধব প্রশাসন গড়ে তোলা।
এই সম্মিলিত প্রচেষ্টাই বাংলাদেশকে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।