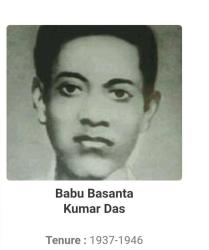ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক নীতি আসলে কী!

সাইফুল খান
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প এমন এক চরিত্র, যিনি একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ঐতিহ্য ভেঙেছেন, অন্যদিকে বৈশ্বিক কূটনীতির রীতি-নীতি উল্টে দিয়েছেন। ট্রাম্পের নীতিকে একক শব্দে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। কিন্তু বিশ্লেষকরা একে বলেন “Transactional Nationalism”, অর্থাৎ আদর্শ নয়, বরং প্রতিটি পদক্ষেপের কেন্দ্রে ছিল বাণিজ্যিক লাভ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক হিসাব এবং জাতীয় স্বার্থের নিরেট বাস্তববাদ।
তার নীতি গুলো আলোচনা সবিস্তারে আসা জরুরী।
“America First” নীতির মূল দর্শন
ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক নীতির ভিত্তি ছিল তার নির্বাচনী স্লোগান “America First”।
এই নীতিতে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বনেতা হিসেবে নয়, বরং একটি স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্র হিসেবে আচরণ করে।
ট্রাম্প বিশ্বাস করতেন, অতীতের প্রেসিডেন্টরা মার্কিন অর্থনীতি, সামরিক ব্যয় ও প্রযুক্তিকে অন্য দেশের জন্য “সস্তায়” বিলিয়ে দিয়েছে।
তাই তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা, সামরিক জোট ও বৈশ্বিক চুক্তির প্রতি প্রকাশ্য সন্দেহ প্রকাশ করেন।
তার বক্তব্য ছিল সরল কিন্তু তীক্ষ্ণ: “আমরা কারো পুলিশ না, কারো দাতা না। আমেরিকা নিজের ঘর আগে ঠিক করবে।”
বহুপাক্ষিকতার পরিবর্তে একক সিদ্ধান্তবাদ
ট্রাম্প জাতিসংঘ, ন্যাটো, ডব্লিউএইচও, এমনকি প্যারিস জলবায়ু চুক্তির মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে “অকার্যকর” বলে আখ্যা দেন।
তিনি বিশ্বাস করেন, এই সংস্থাগুলো মার্কিন করদাতাদের অর্থে চলে, কিন্তু আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করে না। ফলে তার প্রশাসন এসব সংস্থা থেকে বেরিয়ে আসে বা অর্থ কমিয়ে দেয়।
এমনকি ইউরোপীয় মিত্রদের সাথেও ট্রাম্প আচরণ করেন যেন তারা “ক্লায়েন্ট” দেশ।
বারবার বলেন- “আমরা তোমাদের রক্ষা করছি, তাই বিল দাও।”
এই মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের নৈতিক অবস্থান দুর্বল করে দেয়। কিন্তু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল ঠান্ডা বাস্তববাদের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।
চীনের সাথে “Trade War” বাস্তববাদ না রক্ষণশীল আতঙ্ক?
ট্রাম্প প্রশাসনের সবচেয়ে আলোচিত অধ্যায় হলো চীনের বিরুদ্ধে বাণিজ্যযুদ্ধ। তিনি চীনের পণ্য আমদানিতে শত শত বিলিয়ন ডলারের শুল্ক আরোপ করেন। প্রযুক্তি খাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন এবং হুয়াওয়ের মতো কোম্পানিকে “নিরাপত্তা হুমকি” ঘোষণা করেন।
তবে এ যুদ্ধ কেবল অর্থনীতির ছিল না।
এ ছিল এক ধরণের টেকনো-ন্যাশনালিস্ট যুদ্ধ, যেখানে প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর, 5G এবং AI সবই আমেরিকার প্রাধান্য রক্ষার অস্ত্র হয়ে ওঠে।
চীনের “Made in China 2025” প্রকল্পকে ট্রাম্প দেখেছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠত্বের সরাসরি চ্যালেঞ্জ হিসেবে।
মধ্যপ্রাচ্যে ট্রাম্প-একদিকে শান্তি, অন্যদিকে আগুন
ট্রাম্প প্রশাসন ইরানকে ঘিরে নেয় “Maximum Pressure” নীতিতে। তিনি ইরান পারমাণবিক চুক্তি (JCPOA) থেকে বেরিয়ে যান। কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন এবং কুদস বাহিনীর প্রধান জেনারেল কাসেম সোলাইমানিকে শান্তিকালীন সময়ে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে নির্লজ্জভাবে হত্যা করেন। যা বিশ্ব কূটনীতিতে ছিল এক ঐতিহাসিক ধাক্কা।
অন্যদিকে, ইসরায়েলের প্রতি ট্রাম্পের সমর্থন একতরফা ও সীমাহীন। জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস সরিয়ে নেন। যা আরব বিশ্বকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তবু ট্রাম্প গর্ব করেন “Abraham Accords” এর জন্য, যেখানে কয়েকটি আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। এখানেই দেখা যায়, ট্রাম্পের নীতি দ্বিমুখী। একদিকে সংঘাত সৃষ্টি, অন্যদিকে শান্তির ব্যবসায়িক চুক্তি।
দক্ষিণ এশিয়া: পাকিস্তান ও ভারতের ভারসাম্য
ট্রাম্পের সময় পাকিস্তানের প্রতি কড়া অবস্থান দেখা যায়। তিনি পাকিস্তানকে “terror safe haven” আখ্যা দেন এবং সহায়তা বন্ধ করেন।
কিন্তু আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের প্রয়োজনে তিনি আবার পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় ফেরেন। এরপর আবার তিনি পাকিস্তানের প্রশংসা শুরু করেন।
ভারতের ক্ষেত্রে, ট্রাম্প ব্যক্তিগত সম্পর্ককে গুরুত্ব দেন। মোদি ও ট্রাম্পের বন্ধুত্বমূলক শো “Howdy Modi” ও “Namaste Trump”ছিল রাজনীতির চেয়ে বেশি “দৃশ্যনির্ভর কূটনীতি।”
কিন্তু বাস্তবে, ভারতের বাণিজ্যিক সুবিধা কাটছাঁট হয় এবং H-1B ভিসা কঠোর হয়। সোজা কথা সম্পর্কের গনেশ উল্টে যায়।
ইউক্রেন ও রাশিয়া - নীরব মিত্রতা?
রাশিয়ার প্রতি ট্রাম্পের নরম অবস্থান বরাবরই বিতর্কিত। তিনি ন্যাটোকে দুর্বল বলেন, কিন্তু পুতিনকে কখনো প্রকাশ্যে সমালোচনা করেন না। অনেকে বলেন, ট্রাম্পের কূটনীতিতে রাশিয়া একপ্রকার ‘অদৃশ্য মিত্র’ হয়ে উঠেছিল।
এই নীরব মিত্রতাই বাইডেন প্রশাসনের সময় ইউক্রেন যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করে। ট্রাম্প আসলে শক্তের ভক্ত।
বিশ্ব নেতৃত্বের ধারণা বদলে দেওয়া
ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগমনের আগে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি একধরনের নৈতিক কর্তৃত্বের ধারণার ওপর দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী যুগে আমেরিকা নিজেকে কেবল একটি রাষ্ট্র হিসেবে নয়, বরং বিশ্বের নৈতিক দিশারি হিসেবে উপস্থাপন করত। “Democracy”, “Human Rights” এবং “Global Leadership” ছিল সেই ঐতিহ্যবাহী পররাষ্ট্রনীতির স্তম্ভ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা নিজেদের দায়িত্ব ভাবতেন বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষা করা, মানবাধিকার নিশ্চিত করা আর দারিদ্র্য বা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোকে পুনর্গঠনে নেতৃত্ব দেওয়া। এই আদর্শিক কাঠামোর ভেতরেই তৈরি হয়েছিল ‘আমেরিকান এক্সসেপশনালিজম’ অর্থাৎ আমেরিকা ভিন্ন, শ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের নৈতিক দিকনির্দেশক।
কিন্তু ট্রাম্পের আগমনে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়। তিনি রাষ্ট্রনেতা হিসেবে আচরণ করেননি ; বরং আচরণ করেন একজন কঠিন ব্যবসায়ীর মতো। তাঁর কাছে পররাষ্ট্রনীতি ছিল একপ্রকার “ডিল-মেকিং প্রক্রিয়া”।যেখানে প্রতিটি সম্পর্ক, প্রতিটি জোট, এমনকি মানবিক সহায়তাও একটি চুক্তির মতো। “আমরা কত দিচ্ছি, তার বিনিময়ে আমরা কী পাচ্ছি?”
এই দৃষ্টিভঙ্গি ঐতিহ্যবাহী কূটনীতির বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। পূর্বতন নেতারা “অঙ্গীকার” বা “দায়িত্ব” এর ভাষায় কথা বলতেন, সেখানে ট্রাম্প ব্যবহার করেন দরকষাকষির ভাষা। তিনি বিশ্বাস করেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কোনো নৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং একটি লেনদেন। তাঁর কাছে ন্যাটো বা জাতিসংঘ কোনো “মূল্যবোধভিত্তিক জোট” নয়, বরং এমন প্রতিষ্ঠান যা আমেরিকার অর্থে টিকে আছে, অথচ আমেরিকার যথাযথ সুবিধা দেয় না।
এই “লেনদেনমূলক কূটনীতি” (Transactional Diplomacy) একদিকে বৈশ্বিক রাজনীতিকে বাস্তববাদী করে তুলেছে। অন্যদিকে নৈতিক নেতৃত্বের ধারণাকে সংকুচিত করেছে। ট্রাম্প বলেন, “আমরা কারো জন্য যুদ্ধ করব না, যদি আমাদের কোনো লাভ না থাকে।” তাঁর এই বক্তব্যে যেন ফুটে ওঠে ২১ শতকের “নিউ রিয়ালিজম”। যেখানে আন্তর্জাতিক রাজনীতি কেবল শক্তি ও স্বার্থের গণিত।
তবে, এই নীতির কিছু ইতিবাচক দিকও ছিল। উদাহরণস্বরূপ, অনেক আমেরিকান নাগরিক দীর্ঘদিন ধরে মনে করতেন যে তাদের করের অর্থ বিদেশে অপচয় হচ্ছে। ট্রাম্প সেই হতাশ মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীকে মনে করিয়ে দিলেন আমেরিকার ট্যাক্সদাতা প্রথমে আমেরিকার জন্যই। তাঁর এই “America First” দর্শন ছিল জনতার অর্থনৈতিক ক্ষোভকে রাজনৈতিক ভাষা দেওয়ার এক উপায়। ফলে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতির জনপ্রিয়তাই তার কূটনৈতিক বাস্তববাদকে খাদ্য জুগিয়েছে।
তবে বিপরীতে, এই মনোভাব বিশ্ব রাজনীতিতে আমেরিকার নেতৃত্বের ঐতিহ্যকে ধাক্কা দেয়। ইউরোপীয় মিত্ররা ট্রাম্পের নীতিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে; তারা হঠাৎ বুঝতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র আর “বড় ভাই” নয় বরং “লেনদেনকারী পার্টনার”। কানাডা, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো দেশগুলো প্রকাশ্যে আমেরিকার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে শুরু করে। এর ফলে তৈরি হয় এক ধরনের “Post-American Order”, যেখানে আমেরিকার নৈতিক নেতৃত্বের জায়গা নিয়ে নেয় সন্দেহ ও অবিশ্বাস।
অন্যদিকে, চীন ও রাশিয়া এই সুযোগকে কৌশলে কাজে লাগায়। ট্রাম্প যখন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করছিলেন, তখন বেইজিং ও মস্কো সেই শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে আসে। ট্রাম্প নিজে হয়তো মনে করেন, তিনি আমেরিকাকে রক্ষা করছেন; কিন্তু বাস্তবে, তাঁর আচরণ বৈশ্বিক নেতৃত্বের কেন্দ্রকে বিভক্ত করেছে এবং নতুন শক্তিগুলোর জন্য ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে।
বাস্তবতা হলো, ট্রাম্পের সময় থেকে বিশ্ব নেতৃত্বের ধারণা একেবারে বদলে গেছে। আগে যেখানে নেতৃত্ব মানে ছিল নৈতিক অবস্থান, কূটনৈতিক পরিপক্বতা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতা। এখন নেতৃত্ব মানে হয়েছে, কে বেশি দরকষাকষি করতে পারে, কে নিজের স্বার্থে সবচেয়ে নির্দয়ভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
তবুও, ইতিহাস হয়তো ট্রাম্পকে একদিক থেকে নতুন বাস্তববাদের প্রবর্তক হিসেবেই মনে রাখবে। তিনি হয়তো নৈতিকতার মুখোশ সরিয়ে দেখিয়েছেন, আধুনিক বিশ্ব আসলে “মূল্যবোধে” নয়, “স্বার্থে” চলে। সেই অর্থে, ট্রাম্প বৈশ্বিক নেতৃত্বকে ধ্বংস করেননি, বরং তাকে এক নির্মম বাস্তবতার আয়নায় দাঁড় করিয়েছেন।
পরিশেষ
ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক নীতি কেবলই যুক্তরাষ্ট্রকেন্দ্রিক, স্বল্পমেয়াদি এবং প্রভাবশালী।
তিনি বিশ্বের কাছে এক ভিন্ন যুক্তরাষ্ট্র দেখিয়েছেন। যে দেশ নেতৃত্ব দিতে নয়, বরং “বিনিময় করতে” চায়।
এর ফল - মিত্রদের মধ্যে অনাস্থা, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে বিভ্রান্তি এবং বিশ্ব রাজনীতিতে এক অনিশ্চয়তার স্থায়ী ছায়া।
তবে, সমর্থকরা বলেন ট্রাম্প অন্তত আমেরিকার স্বার্থে সোজাসাপট। তিনি কূটনৈতিক ভণ্ডামি ভেঙেছেন, প্রশাসনিক মুখোশ সরিয়েছেন।
আর বিরোধীরা বলেন, তিনি বিশ্বের ভারসাম্য নষ্ট করেছেন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে একাকী করে তুলেছেন।
এক কথায় বলা যায়-
ট্রাম্পের আন্তর্জাতিক নীতি হলো আদর্শের নয়, বরং প্রভাব ও মুনাফার রাজনীতি।
যেখানে কূটনীতি এক ধরনের “ডিল”, আর বিশ্ব নেতৃত্ব একপ্রকার “ব্র্যান্ডিং”।
.png)