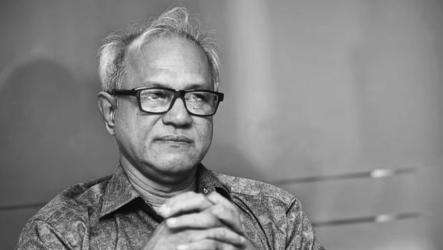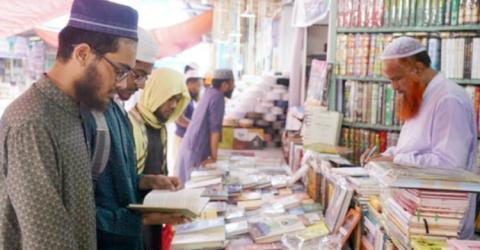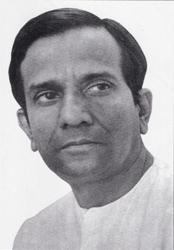বাংলাদেশের বিপন্ন ভাষা: হারিয়ে যাওয়া সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য

সংগ্রাম দত্ত
বাংলাদেশ একটি বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির দেশ। এই ভূমিতে বহু প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বসবাস করছে। প্রথমে এখানে বাস করতেন অনার্য জনগণ। পরে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর মানুষ এ অঞ্চলে আগমন করেন। আর্যদের আগমনের পর এই অঞ্চলে একটি মিশ্রিত বা সংকর সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর আগমন বাংলা সংস্কৃতিকে বৈচিত্র্যময় করেছে।
বাংলাদেশে বাংলা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা। তবে দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রায় ৪০টি ভাষা এবং ৫০টি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের ভাষা বাংলার সাংস্কৃতিক রঙ বাড়িয়েছে।
গত ১ মার্চ ২০২৫ দি ডেইলি স্টার \"দেশে হারিয়ে যাচ্ছে যে কয়েকটি ভাষা\" শীর্ষক এক প্রতিবেদন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান লিখেছেন যে, দেশে বাংলাসহ যে ৪১টি ভাষার সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো- বাংলা, বম, কন্দ, চাক, চাকমা, ঠার, মান্দি, হাজং, খাসি, খাড়িয়া, খিয়াং, খুমি, কোচ, কোল, লসাই, মারমা, ম্রো, অহমিয়া, মণিপুরি মৈতৈ, মণিপুরি বিষ্ণুপ্রিয়া, মুন্ডা, কানপুরি, মাহলে, কুড়ুখ, পাংখোয়া, মালতো, পাত্র/লালেং, রাখাইন, সৌরা, মাদ্রাজি, সাঁওতালি, তেলুগু, তঞ্চঙ্গ্যা, ককবরক, নেপালি/গুর্খা, রেংমিটচা, কোডা, লিঙ্গাম, উড়িয়া ও সাদরি। এরমধ্যে ১৪ টি ভাষা বিপন্ন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে ।
ভাষার বিপন্নতার ধাপ
ভাষার জীবন্ততা পরিমাপের জন্য বিশেষজ্ঞরা বিভিন্ন ধাপ নির্ধারণ করেছেন। স্টিফেন ওয়ার্ম অনুযায়ী ভাষার বিপন্নতা পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়:
সম্ভাব্য বিপন্ন: জনগোষ্ঠী ভাষা ব্যবহার করতে চায়, কিন্তু বসতি বা শিক্ষা ক্ষেত্রে বাধার কারণে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।
বিপন্ন: তরুণ প্রজন্ম ভাষা ব্যবহার করে না বা শিখতে চায় না, বাড়িতে বা স্কুলে ব্যবহার কম।
সংকটপূর্ণভাবে বিপন্ন: কেবল বয়স্করা ভাষা বলতে পারে, সামাজিকভাবে ভাষার মর্যাদা কম।
প্রায় বিলুপ্ত: খুব অল্পসংখ্যক বয়স্ক লোকের মধ্যে সীমিত ব্যবহার।
বিলুপ্ত: কোনো জীবিত ব্যবহারকারী নেই।
ফিশম্যান স্কেলে (GIDS) ভাষার বিপন্নতা আরও সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ ভাষা ফিশম্যান স্কেলে বিপন্ন। উদাহরণস্বরূপ:
বিপন্ন: ককবরক, বিষ্ণুপ্রিয়-মণিপুরী, কুরুখ, বম।
প্রায় বিলুপ্ত: রেংমিটচা, সৌরা।
উচ্চ স্তরের বিপন্নতা: খারিয়া (খাড়িয়া), কোডা, মুন্ডারি, কোল, মালতো, কন্দ, খুমি, পাংখোয়া, চাক, খিয়াং, লালেং/পাত্র, লুসাই।
সংকটাপন্ন ভাষার বিস্তারিত অবস্থা:
রেংমিটচা
রেংমিটচা ভাষার বর্তমানে কোনো পরিবারকেন্দ্রিক ব্যবহার নেই। জানা যায়, মাত্র ৪-৫ জন বেঁচে আছে, যাঁরা আলাদা পরিবারে থাকেন। কথা বলার জন্য পরিবারের অন্য সদস্য নেই। লেখক ও গবেষক ইয়াংঙান ম্রো একটি অভিধান ‘মিটচ্যা তখক’ প্রণয়ন করেছেন, যেখানে প্রায় ৩,০০০ শব্দ সংকলিত হয়েছে।
সৌরা
মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে বাস করে। বাংলাদেশে মোট ৭০টি পরিবার থাকলেও শুধুমাত্র ৪-৫ জন ভাষা বলতে পারে। বাকি সবাই আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে। ভারতের উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু রাজ্যে এই ভাষার লিখিত রূপ আছে, কিন্তু বাংলাদেশে নেই।
লালেং/পাত্র
সিলেট জেলার ২৩টি গ্রামে বসবাসরত পাত্র সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা ২০৩৩ জন। শিশু প্রজন্ম ভাষা শিখছে না এবং পরিবারের ৫০% অংশে বাংলা অনুপ্রবেশ ঘটেছে। পাত্র সম্প্রদায় সচেতন হয়ে সেনাপতিটিলা গ্রামে পাত্র ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র চালু করেছে।
খারিয়া
খারিয়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আনুমানিক ৫,৭০০ জন । তারা মূলত সিলেট বিভাগের শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ, চুনারুঘাট , মাধবপুর উপজেলার চা বাগান এলাকায় বসবাস করে।
এই ভাষার অবস্থা খুবই নাজুক। বর্তমানে শ্রীমঙ্গল উপজেলার বর্মাছড়া চা বাগানের সাবলীলভাবে
মাত্র ২ জন বয়স্ক নারী খারিয়া ভাষায় কথা বলতে পারেন। তাঁদের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে খারিয়া ভাষার কোনো জীবিত বক্তা থাকবে না। ফলে এই ভাষা বাংলাদেশের মাটিতে পুরোপুরি বিলুপ্ত হবে।
মালতো
রাজশাহী, নাটোর ও পাবনার মাল পাহাড়ি সম্প্রদায় কিছুদিন আগে পর্যন্ত মালতো ভাষায় কথা বলতো। বর্তমানে তারা সাদরি ভাষায় কথা বলে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারিতে জনসংখ্যা ছিল ১৮৫৩ জন।
কন্দ
বাংলাদেশের ১২টি উপজেলায়, ৩০টি চা বাগানে প্রায় ৫৩৯টি কন্দ পরিবার বসবাস করে। গবেষণায় দেখা যায়, মাত্র ১% মানুষ কন্দ ভাষায় কথা বলতে পারে, শিশু প্রজন্ম প্রায় শিখছে না।
ওঁরাও / কুঁডুখ
উত্তরবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে ৭৫ হাজার জন বসবাস করেন, কিন্তু মাত্র ২৫-৩০ হাজার কুঁডুখ ভাষায় কথা বলে।
ভাষা সংরক্ষণের প্রয়াস
ভাষার অবক্ষয় মানে সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক সম্পদের অপূরণীয় ক্ষতি। ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রস্তাব করেন:
নথিবদ্ধকরণ: শব্দ, বাক্য, কাব্য ও কাহিনী সংরক্ষণ
পুনরুজ্জীবন: ভাষা চর্চা ও শেখার কার্যক্রম
লিপি সৃষ্টি ও শিক্ষা: মাতৃভাষায় লিখিত পাঠ্যক্রম
শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তি: স্কুল, কলেজে ভাষার ব্যবহার
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন: ভাষাভাষী সম্প্রদায়ের মর্যাদা বৃদ্ধি
আইনগত অধিকার: মাতৃভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় সহায়তা
ডেভিড ক্রিস্টালের মতে, ভাষা মর্যাদা ও প্রচারের মাধ্যমে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদের ৩০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষা শেখা ও ব্যবহার করা তাদের অধিকার।
উপসংহার: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা হারিয়ে যাওয়ার পথে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা নিশ্চিত না হলে এই ভাষাগুলো চিরতরে বিলুপ্ত হতে পারে। তাই ভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, নথিবদ্ধকরণ এবং লিপি তৈরি কার্যক্রম নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
ভাষার বিপন্নতা রোধ করা মানে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। প্রতিটি ভাষা সমান মর্যাদা ও গুরুত্বের দাবি রাখে।